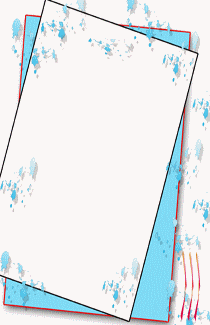নূরে আলম সিদ্দিকী :সন্দেহাতীতভাবে বিএনপি একটি বিশাল জনগোষ্ঠীর প্রতিনিধিত্ব করে। আওয়ামী লীগ -বিরোধী জনতায় এককভাবে বিএনপির সমর্থন জোগায়। বেগম খালেদা জিয়া আজ নানা রোগে জর্জরিত। বয়সের ভারে রোগক্লিষ্ট শরীরে তিনি আজ নিস্তব্ধ ও নিস্পৃহ প্রায়। ইচ্ছা থাকলেও সক্রিয় রাজনীতিতে তাঁর অংশগ্রহণ অসম্ভব প্রায়। অন্যদিকে বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান আজ প্রবাসী। টেলিফোনের মাধ্যমেই রাজনীতি নিয়ন্ত্রণে তিনি সচেষ্ট। তিনি বাংলাদেশে আসতে নারাজ। এলেই তাকে কারাদ- ভোগ করতে হবে, এ আশঙ্কা তাকে পরবাসে অবরুদ্ধ করে রেখেছে। অথচ তিনি এলে, অকাতরে ও সগৌরবে কারাবরণ করলে আন্দোলন কতখানি শক্তিশালী হতো বিএনপির নেতৃত্ব তা হৃদয়ঙ্গম করতে অক্ষম। আমি আমার বহু নিবন্ধে সবিনয়ে উল্লেখ করেছি, ১৯৫৮ সালে সামরিক শাসন জারির পর বঙ্গবন্ধুসহ আমরা কেউই কারাবরণকে এড়িয়ে চলিনি। বরং গর্বিত চিত্তে অকুতোভয়ে সব নির্যাতন-নিপীড়ন সহ্য করে তিল তিল করে আন্দোলনের পটভূমি তৈরি করেছি। ১৯৬৬ সালে তদানীন্তন পাকিস্তানের রাজনীতিতে স্বায়ত্তশাসন থেকে স্বাধিকারের সোপান বিনির্মিত হয় ছয় দফা কর্মসূচির মাধ্যমে। আমি বারবার উল্লেখ করেছি, ছয় দফা দেওয়ার পূর্বকালীন বঙ্গবন্ধু এ দেশের অন্যান্য নেতার সমকক্ষ ছিলেন। তখন এনডিএফই হোক কপই হোক, সব আন্দোলনের যোগসূত্র রচিত হতো সম্মিলিতভাবে। এককভাবে রাজনীতির পথপরিক্রমণের উদ্যোগ, উৎসাহ ও নির্দেশনা আসে ছয় দফার আলোক বিচ্ছুরণের পর।
তদানীন্তন পাকিস্তানের রাজনীতিতে স্বায়ত্তশাসন থেকে স্বাধিকারের আন্দোলনের যে অধ্যায় রচিত হয়, তার সোপান তৈরি করেছিল ছয় দফা। পাকিস্তানের রাজনৈতিক আন্দোলনে পূর্ব পাকিস্তানের অংশীদাররাও স্বায়ত্তশাসনের দাবিতে সোচ্চার ছিলেন। সে সময় পশ্চিম পাকিস্তানে একটি সর্বদলীয় রাজনৈতিক বৈঠক অনুষ্ঠানের প্রাক্কালে যখন পাকিস্তানব্যাপী আইয়ুব শাহির উৎখাতের লক্ষ্যে একটি সর্বদলীয় আন্দোলনের কর্মসূচি গৃহীত হচ্ছিল, সেই গোলটেবিলে যোগ দিয়ে তখনকার পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক শেখ মুজিব ওই রাউন্ডটেবিল কনফারেন্সেই ছয় দফা কর্মসূচিটি পেশ করেন। সর্বদলীয় সংগ্রাম পরিষদ তো বটেই পাকিস্তান আওয়ামী লীগ, এমনকি পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগও চমকে ওঠে ছয় দফা  কর্মসূচি অবলোকনে। আওয়ামী লীগের একটি বিরাট অংশ ওই কর্মসূচিকে হৃদয়ঙ্গম করতে পারেনি। প্রথমত মেনেও নেয়নি। তখন পাকিস্তান আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় সভাপতি ছিলেন নবাবজাদা নসরুল্লাহ খান ও সাধারণ সম্পাদক সোহরাওয়ার্দী সাহেবের প্রধানমন্ত্রিত্বকালীন শিক্ষামন্ত্রী জহির উদ্দিন আহমদ। কেন্দ্রীয় আওয়ামী লীগ ছয় দফা কর্মসূচিকে প্রায় নাকচই করে দেয়। কাগমারী সম্মেলনের পর পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সভাপতি হন মাওলানা আবদুর রশীদ তর্কবাগীশ। তাঁর কনিষ্ঠ পুত্র সৈয়দ শামসুল আলম হাসু সাহেব আমার খুব ঘনিষ্ঠজন ছিলেন। সেই সুবাদে আমি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের হল থেকে তার ওয়ারীর বাসায় গিয়ে চুটিয়ে আড্ডা দিতাম। কখনো কখনো রাতে থেকেও যেতাম। মাওলানা আবদুর রশীদ তর্কবাগীশ আমাকে পুত্রপ্রতিম স্নেহ করতেন হাসুর সঙ্গে আমার আন্তরিকতার নিরিখেই নয়, ব্যক্তিগত বিবেচনায়ও তিনি আমাকে পুত্রপ্রতিমই জানতেন। তাঁর অপত্যস্নেহ ও গভীর মমতাময় আন্তরিকতা আমাকে এতটাই বিমুগ্ধ করত যে, আমি তাঁর বাসায় গেলে তাঁর সঙ্গে দেখা না করে আসতাম না। বঙ্গবন্ধু ছয় দফা দেওয়ার পর তাঁর পুত্র শামসুল আলম হাসুর সঙ্গে মিলে একান্ত অন্তরঙ্গ মুহূর্তে আমি তাঁকে ছয় দফা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেছিলাম।
কর্মসূচি অবলোকনে। আওয়ামী লীগের একটি বিরাট অংশ ওই কর্মসূচিকে হৃদয়ঙ্গম করতে পারেনি। প্রথমত মেনেও নেয়নি। তখন পাকিস্তান আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় সভাপতি ছিলেন নবাবজাদা নসরুল্লাহ খান ও সাধারণ সম্পাদক সোহরাওয়ার্দী সাহেবের প্রধানমন্ত্রিত্বকালীন শিক্ষামন্ত্রী জহির উদ্দিন আহমদ। কেন্দ্রীয় আওয়ামী লীগ ছয় দফা কর্মসূচিকে প্রায় নাকচই করে দেয়। কাগমারী সম্মেলনের পর পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সভাপতি হন মাওলানা আবদুর রশীদ তর্কবাগীশ। তাঁর কনিষ্ঠ পুত্র সৈয়দ শামসুল আলম হাসু সাহেব আমার খুব ঘনিষ্ঠজন ছিলেন। সেই সুবাদে আমি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের হল থেকে তার ওয়ারীর বাসায় গিয়ে চুটিয়ে আড্ডা দিতাম। কখনো কখনো রাতে থেকেও যেতাম। মাওলানা আবদুর রশীদ তর্কবাগীশ আমাকে পুত্রপ্রতিম স্নেহ করতেন হাসুর সঙ্গে আমার আন্তরিকতার নিরিখেই নয়, ব্যক্তিগত বিবেচনায়ও তিনি আমাকে পুত্রপ্রতিমই জানতেন। তাঁর অপত্যস্নেহ ও গভীর মমতাময় আন্তরিকতা আমাকে এতটাই বিমুগ্ধ করত যে, আমি তাঁর বাসায় গেলে তাঁর সঙ্গে দেখা না করে আসতাম না। বঙ্গবন্ধু ছয় দফা দেওয়ার পর তাঁর পুত্র শামসুল আলম হাসুর সঙ্গে মিলে একান্ত অন্তরঙ্গ মুহূর্তে আমি তাঁকে ছয় দফা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেছিলাম।
মাওলানা আবদুর রশীদ তর্কবাগীশ সাহেবের একটা গৌরবোজ্জ্বল সূর্যস্নাত অতীত আছে। ১৯৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি যখন ভাষা আন্দোলনকারীদের ওপর গুলিবর্ষিত হয় তখন তর্কবাগীশ সাহেব প্রাদেশিক সংসদের সদস্য ছিলেন। তিনি সংসদে একটি জ্বালাময়ী বক্তৃতা দিয়ে আন্দোলনকারীদের সঙ্গে মিছিলে অংশ নেন এবং আন্দোলনের প্রতি প্রতীতি জানিয়ে একটি অগ্নিঝরা ভাষণ দেন। তখন থেকেই তিনি বাঙালি জাতির অধিকার আদায়ে প্রদীপ্ত সারথি হিসেবে প্রতিভাত হয়ে ওঠেন। বঙ্গবন্ধু ছয় দফা দেওয়ার পর যখন নামিদামি নেতারা বিব্রত ও বিপর্যস্ত, অনেকে দোটানায় আচ্ছন্ন তখন গৌরবদীপ্ত চিত্তে উদ্ধত মানসিকতায় অকাতরে অম্লান হৃদয়ে মাওলানা আবদুর রশীদ তর্কবাগীশ সাহেব ছয় দফার প্রতি তাঁর উচ্চকিত উদ্বেলিত চিত্তের নিঃশর্ত সমর্থন ঘোষণা করেন।
তার পরের ঘটনা আরও বিস্ময়কর। পরবর্তী সম্মেলনে তখনকার শেখ মুজিবুর রহমান আওয়ামী লীগের সভাপতি নির্বাচিত হলেন আবদুর রশীদ তর্কবাগীশ সাহেবের স্থলে। আমি বিস্মিত হই এবং বিদগ্ধচিত্তে অনুভব করি, মওলানা ভাসানী কাগমারীর সম্মেলনে ন্যাপ গঠন করার পর হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর কি সুচিন্তিত সিদ্ধান্তই না ছিল তখনকার প্রাদেশিক আওয়ামী লীগের সভাপতি হিসেবে আবদুর রশীদ তর্কবাগীশ সাহেবকে নির্ণয় করা। আমি দুটি সময়ই মাওলানা তর্কবাগীশ সাহেবের একান্ত সান্নিধ্যে তাঁর পুত্রদের সামনে তাঁর প্রতিক্রিয়া জানতে চেয়েছি। তিনি সহাস্য বদনে অম্লানচিত্তে তাঁর হৃদয়ের আবিরমাখা সমর্থন প্রকাশ করেছেন। তিনি অসংখ্যবার বলেছিলেন, আমরা যা পারিনি শেখ মুজিব তা পেরেছে। এ দেশের মানুষকে সাফল্যের সৈকতে পৌঁছে দিয়ে তাদের কাক্সিক্ষত স্বপ্ন পূরণ করার কঠিন দায়িত্ব পালন সফলভাবে শেখ মুজিবই করতে পারবে। এ কথাগুলো বলা প্রয়োজন এ কারণে, তখন শেখ মুজিবুর রহমান আন্দোলন ও নির্বাচনকে সমান্তরালভাবে এগিয়ে নিয়ে গেছেন। নির্বাচনকে তিনি আন্দোলনের অন্যতম হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করেছেন। নির্বাচনের মাধ্যমে তিনি গণসংযোগ করেছেন, জনগণের সন্নিকটে সংগঠনকে নিয়ে গেছেন। নগরে-বন্দরে, গ্রামে-গঞ্জে সরকারবিরোধী আন্দোলনের বীজ বপন করেছেন এবং নানা সভা-সমিতি ও মিছিলের মাধ্যমে জনগণের চিন্তাকে শানিত করেই একটি অনির্বাণ মননশীলতা গড়ে তুলতে সক্ষম হয়েছেন।
১৯৫৪ সালের নির্বাচনে হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী, শেরেবাংলা এ কে ফজলুল হক ও মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানীকে একটি একক নির্বাচনী আন্দোলনের যোগসূত্রে গ্রোথিত করার অন্যতম কারিগর ছিলেন তখনকার শেখ মুজিব। ’৫৪ সালের নির্বাচনে কেউই বুঝতে পারেনি পাকিস্তান অর্জনকারী সংগঠন মুসলিম লীগ সাত বছরের মাথায় এমন ভরাডুবি দেখবে। তখনকার পূর্ব পাকিস্তানের মুখ্যমন্ত্রী নূরুল আমিন সাহেবও যুক্তফ্রন্টের প্রার্থী ছাত্রনেতা খালেক নেওয়াজের কাছে শোচনীয়ভাবে পরাজিত হন। পাকিস্তান অর্জনের সাত বছরের মাথায় সেটি ছিল একটি বিস্ময়কর গণ-অভ্যুত্থান। ’৫৪-এর নির্বাচনের মাধ্যমেই সেই অভ্যুত্থান ঘটাতে সক্ষম হয়েছিলেন শেরেবাংলা, শহীদ সোহরাওয়ার্দী ও মওলানা ভাসানী। গ্রামেগঞ্জে নগরে-বন্দরে উল্কার মতো ছুটে বেড়িয়েছেন বাংলার স্বাধীনতা আন্দোলনের পথিকৃৎ শেখ মুজিব। সামনে তাঁর নেতা হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী। শেরেবাংলা ও মওলানা ভাসানীর কাউকেই তিনি ছোট করেননি, খাটো করেননি কারও সম্মান। তার পরও নির্বাচনে অংশগ্রহণের দুর্দমনীয় অভিযানে তাঁর নেতৃত্ব বিকশিত হয় প্রদীপ্ত সূর্যরশ্মির মতো। আজ যারা বক্তৃতা-বিবৃতিতে নির্বাচনের প্রশ্নে নেতিবাচক মনোভাব উদ্গিরণ করেন, তারা বিস্মৃত হন, নির্বাচন বর্জন করলে জনগণের সঙ্গে দূরত্বই বৃদ্ধি পায়। আর আন্দোলন করতে হলে তার অনিবার্য শর্ত হলো জনগণের সম্পৃক্ততা এবং জনগণই হয় তার নিয়ামক শক্তি।
১৯৬২ সালের নির্বাচনটিও বেসিক ডেমোক্র্যাসির মাধ্যমে সংঘটিত হয়। এটি অতি সহজেই অনুমেয় ছিল যে, ওই নির্বাচনে পরাজয় অনিবার্য। তবু আওয়ামী লীগসহ তৎকালীন কোনো রাজনৈতিক সংগঠনই নির্বাচন বর্জন করেনি বা নির্বাচনবিমুখ কোনো মননশীলতাও তুলে ধরেনি। ’৬৪ সালের নির্বাচনে নিশ্চিত পরাজয় জেনেও মাদার-এ-মিল্লাতকে প্রার্থী করে আইয়ুব খানের বিরুদ্ধে লড়াই করেছিল তখনকার সব গণতান্ত্রিক শক্তি। মৌলিক গণতন্ত্রের ওই নির্বাচনে জয় নিতান্তই অসম্ভব ছিল। মাদার-এ-মিল্লাত বিজয়ী হননি, তবে ১৯৭০ সালের নির্বাচনে গণতান্ত্রিক শক্তি আওয়ামী লীগের বিজয়ের সোপান রচিত হয়েছিল ’৬৪-এর সেই হেরে যাওয়া নির্বাচনের মাধ্যমে। নির্বাচন কেবল ক্ষমতা দখলের সোপান নয়, গণতান্ত্রিক অবকাঠামোর একটি শক্তিশালী স্তম্ভ। নির্বাচনে অংশগ্রহণের মাধ্যমে অতি সহজে জনগণের সান্নিধ্যে আসা যায়। নিজেদের যেকোনো গণতান্ত্রিক কর্মসূচি জনগণের কাছে পৌঁছে দেওয়া যায়, জনগণকে কাছে টেনে জনগণের গণ-আন্দোলন তৈরি করা যায়। নির্বাচন পাশ কাটিয়ে বা নির্বাচনের প্রশ্নে নেতিবাচক মনোভাব পোষণ করে কোনো অবস্থায়ই জনসম্পৃক্ততা গড়ে ওঠে না। আজকের বিরোধী দলের যারা আন্দোলনের কথা ভাবেন, তারা যদি সত্যিকার অর্থেই কোনো সফল গণতান্ত্রিক আন্দোলনের উদ্যোক্তা হতে চান, তাহলে সব রোমান্টিসিজমের ছোঁয়াচে রোগ তাদের পরিহার করতে হবে। সত্যিকার আন্দোলনের সঙ্গে রোমান্টিসিজমের কোনো যোগসূত্র থাকে না। গণতন্ত্রে বিশ্বাসী যেকোনো মানুষ জনগণের সম্পৃক্ততাকে গুরুত্ব দিয়ে থাকে। জনগণ যদি কোনো কর্মসূচি থেকে নেতৃত্বের অদূরদর্শিতার কারণে দূরে সরে যায় বা ছিটকে পড়ে অথবা হতাশাগ্রস্ত হয়ে অনিশ্চয়তার অন্ধকারে নিপতিত হয় তাহলে সফল গণতান্ত্রিক আন্দোলন গড়ে ওঠে না। সাফল্যের সৈকতে পৌঁছাও সম্ভব হয় না। আজ বিএনপি যদি আসন্ন নির্বাচনটিকে এড়িয়ে গিয়ে যেকোনো স্লোগানে আন্দোলনের রোমান্টিসিজমে ভাসতে চায় তাহলে তারা অনিশ্চয়তার ঊর্মিমালায় নিমজ্জিত হয়ে যাবে, এটা সুনিশ্চিত। গণতন্ত্রের মূল কথাই হচ্ছে- ‘জনগণই সকল ক্ষমতার উৎস’। সেই জনগণকে পাশ কাটিয়ে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার কথা কল্পনাও করা যায় না।
যেহেতু বেগম খালেদা জিয়া আজ একান্তই অসুস্থ, মিছিলের সম্মুখভাগে থেকে নেতৃত্ব দেওয়া তাঁর পক্ষে অসম্ভব আর অন্যদিকে বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান প্রবাসী, তাই প্রশ্ন হলো, অন্য যেসব নেতৃত্ব মাঠে রয়েছেন তারা জনগণকে সার্বিক অর্থে কতটুকু কাছে টানতে পারবেন। সেটাই আজকে রাজনীতির সবচেয়ে বড় প্রশ্ন। যদি সত্যিকার অর্থেই এ দেশে একটি ফলপ্রসূ রাজনৈতিক আন্দোলন গড়ে তুলতে হয়, তাহলে তাদের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যানকে অবশ্যই বাংলাদেশে আসতে হবে। অনেকে বলবেন তাহলে তিনি তো গ্রেফতার হয়ে যাবেন, কারাগারই তার ঠিকানা হবে। তার উত্তরে আমি বলব, কারাগার ঠিকানা হলে আন্দোলন শুধু বেগবানই হবে না বিস্ফোরিত হবে, আগ্নেয়গিরির গলিত লাভার মতো প্রজ্বলিত হবে। মেঘে মেঘে ঘর্ষণ না লাগলে যেমন বিদ্যুৎ চমকায় না, মেহেদিকে না পিষলে যেমন লাল রং বিচ্ছুরিত হয় না তেমনি নেতা নির্যাতন মোকাবিলা না করলে, নির্যাতনের মুখে দাঁড়িয়ে পাঞ্জা না লড়লে আন্দোলন ফলপ্রসূ হয় না। বঙ্গবন্ধুর বিরুদ্ধে যদি আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা না হতো, বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে আমরা অসংখ্য রাজনৈতিক কর্মী যদি কারাগারের নিঃসঙ্গ যন্ত্রণাকে আলিঙ্গন না করতাম, তাহলে ’৬৯-এর গণঅভ্যুত্থানের পটভূমি তৈরি হতো না। ’৭০-এর নির্বাচনের নিরঙ্কুশ ম্যান্ডেটও বঙ্গবন্ধু পেতেন না। শুধু আমার নয়, সে সময়ের প্রতিটি রাজনৈতিক ব্যক্তিরই সুস্পষ্ট উপলব্ধি হলো, আন্দোলন করতে হলে নেতৃত্বকে যেকোনো নির্যাতন-নিপীড়নের মুখে অকুতোভয়ে মেরুদ- খাড়া করে মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে হবে। নির্যাতন সহ্য না করলে আন্দোলনে প্রাণ সঞ্চারিত হয় না। আন্দোলনও চাই, কারাগারকেও ভয় পাই- এ দুটি একসঙ্গে চলতে পারে না। আর চালাতে চাইলে এখনকার মতো আন্দোলনও ঢিমেতালে চলবে। সংগ্রাম কোনো তবলার বোল নয়, সংগ্রামের সঙ্গে ত্যাগের একটা অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক রয়েছে। ত্যাগ ছাড়া, নির্যাতনকে অকুতোভয়ে সহ্য করা ছাড়া, যেকোনো চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করার অমিতবিক্রম সাহস ছাড়া কোনো আন্দোলন সফল হয় না, বড় কোনো রাজনৈতিক অর্জনও সম্ভব হয় না। এ বাস্তবতাটাকে বিরোধী রাজনৈতিক সত্তারা যত তাড়াতাড়ি অনুধাবন করবেন, তত তাড়াতাড়ি তাদের আন্দোলন সফলতার দিকে মোড় নেবে। এখানে বিনম্রচিত্তে আমি উল্লেখ করতে চাই, ১৯৯৬ ও ২০০৬ সালে এই বিএনপির সরকারের বিরুদ্ধেই আওয়ামী লীগ সফল গণ-আন্দোলন গড়ে তুলেছিল। আওয়ামী লীগ কর্মীনির্ভর দল। মাঠে-ময়দানে, মিছিলে, সভায় আওয়ামী লীগের কর্মীরা লড়াকু সৈনিক। বিএনপিতে অসংখ্য নামিদামি নেতা রয়েছেন, অনেক সাবেক মন্ত্রী-সংসদ সদস্য রয়েছেন। আবার অন্যদিকে অনেক মামলায় জুড়ে দেওয়া আসামিও রয়েছেন। কিন্তু রাজনৈতিক কারণে অকাতরে অম্লান বদনে নিজেকে উৎসর্গ করার, নির্যাতন-নিগ্রহ অগ্রাহ্য করে গণসম্পৃক্ততা গড়ে তোলার আগ্রহের অভাব আছে। বিএনপির জন্য আজ প্রয়োজন একদল অকুতোভয় কর্মীর, যারা কোনো নির্যাতনকে গ্রাহ্য করবে না। এটি সর্বজনবিদিত যে, বিএনপি ভোট পাওয়ার সংগঠন, আন্দোলন করার সংগঠন নয়।
ছয় দফা দেওয়ার পর বঙ্গবন্ধু আমাদের মতো একগুচ্ছ অপরাজেয় দুঃসাহসী কালজয়ী কর্মী পেয়েছিলেন এবং এ শক্তিতেই তিনি ’৭০-এ নির্বাচনে ঐতিহাসিক বিজয়টি অর্জন করতে পেরেছিলেন। এ কথা সন্দেহাতীতভাবে বলা চলে, ছয় দফা দেওয়ার পর যে নেতৃত্বের পটভূমিকা তৈরি হয়, সেই নেতৃত্ব পূর্ণ কর্তৃত্বের অধিকারী হয় ’৭০-এর গণম্যান্ডেট লাভের পর। ছয় দফা প্রদানের আগে বঙ্গবন্ধু এ দেশের অনেক নেতার একজন ছিলেন। তখন সর্বদলীয়ভাবে আন্দোলন গড়ে উঠত। বিবৃতিও আসত ১১ নেতার। তখনকার শেখ মুজিব এই ১১ জনের অন্যতম ছিলেন। ’৭০-এর নির্বাচন বঙ্গবন্ধুকে বাঙালির পূর্ব পাকিস্তানের একক নেতৃত্বের গৌরবের অধিকারী করে আর তখনকার পাকিস্তানের নেতৃত্ব যখন বঙ্গবন্ধুকে অস্বীকার করে জুলফিকার আলী ভুট্টোর পরামর্শে বাংলার মুজিবকে পাশ কাটিয়ে যেতে চেষ্টা করে তখনই সারা দেশ প্রতিবাদের বজ্রনির্ঘোষে গর্জে ওঠে। বাংলাদেশ জ্বলন্ত ভিসুভিয়াসে পরিণত হয়।
তাই আন্দোলন করতে হলে নির্বাচন একটা দুর্দমনীয় মাধ্যম হয়ে উঠতে পারে। নির্বাচন মানে আপসকামিতা নয়। নির্বাচন মানেই জনগণের সঙ্গে সম্পৃক্ততা, জনগণের সঙ্গে রাখীবন্ধনের একটা অপূর্ব সুযোগ। কেউ জেগে ঘুমালে তাকে জাগানো কঠিন। অবস্থাদৃষ্টে মনে হয়, বিএনপি অনেকটা জেগেই ঘুমাচ্ছে। এ দেশের জনগণ যদি সত্যিকার অর্থেই আওয়ামী লীগের শাসনে অতিষ্ঠ হয়ে থাকে, তাহলে সন্দেহাতীতভাবে আগামী নির্বাচনে তারা আওয়ামী লীগের বিরুদ্ধে বিএনপিকে ভোট দেবে। আগামী নির্বাচনে বিএনপি যদি সংখ্যাগরিষ্ঠ সংসদ সদস্য না-ও পায়, তবে একটা বিরাট শক্তিশালী বিরোধী দল গড়ে তুলতে পারবে, এতে তো কোনো সন্দেহ নেই। তাদের যে বিভাগীয় সমাবেশগুলো হচ্ছে, সেখানে তারা সরকারের ভুলত্রুটিগুলো পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে শুধু তুলেই ধরবেন না, বরং আওয়ামী লীগের ভুলের বিপরীতে আগামীতে সরকারে এলে তারা কী ধরনের কর্মসূচি বাস্তবায়ন করবেন, তা-ও তাদের তুলে ধরতে হবে। এটি সৃজনশীল বিরোধী দলের দায়িত্ব। একটি উন্নয়নশীল দেশে বিরোধী দলকে শুধু বিরোধিতার জন্য বিরোধিতা নয়, জনগণের সামনে তাদের কর্মসূচিটিও উপস্থাপন করতে হবে। তারা কীভাবে দেশ গড়বে, দেশের বিনির্মাণে ও সার্বিক উন্নয়নে তাদের চিন্তা ও পরিকল্পনা জনগণকে সম্যকভাবে অবহিত হতে হবে। যেসব দেশে গণতন্ত্র স্থায়িত্ব লাভ করেছে আমেরিকা, ইংল্যান্ড এমনকি ভারতবর্ষেও বিকল্প কর্মসূচি দিয়েই সরকার ও বিরোধী দলের কর্মযজ্ঞ চলে। শুধু নেতিবাচক কথায় সেখানে রাজনীতি পরিচালিত হয় না। দেশের উন্নয়ন, তারপর রাষ্ট্রনীতি, স্বাস্থ্য, শিক্ষা, অর্থনীতি অঙ্গনগুলোই পরিপাটিভাবে সাজিয়ে জনগণের সামনে তুলে ধরতে হয়। জনগণ তখন কর্মসূচির আলোকেই তাদের সমর্থন নির্ধারণ করতে পারে। লাগাতার নির্বাচন বর্জনের তর্জন-গর্জন, ইঙ্গিত-ইশারা বিএনপির সপক্ষে থাকা জনগোষ্ঠীকে নিরন্তর নিরুৎসাহ করবে এবং যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হতে ইন্ধন জোগাবে। রাজনৈতিক বিবেচনায় এটি কোনো দেশাত্মবোধে উজ্জীবিত রাজনৈতিক দলের কাম্য হতে পারে না। এটাই নিরেট বাস্তব, আওয়ামী লীগের প্রবল গণ-আন্দোলনের মুখে ১৯৯৬ ও ২০০৬ সালে বিএনপি সরকারকে পদত্যাগ করতে হয়েছিল এবং তারা নিরপেক্ষ তত্ত্বাবধায়ক সরকারের দাবি মেনে নিতে বাধ্য হয়েছিল। কিন্তু এ রকম একটি গণ-আন্দোলন সৃষ্টি করার শক্তি বিগত বছরগুলোয় বিএনপি প্রমাণ করতে পারেনি।
তাই মোদ্দা কথা হলো, নির্বাচন বর্জন নয় বরং নির্বাচনকে জনসম্পৃক্ততার মাধ্যম হিসেবে গ্রহণ করে আন্দোলনেরও অবলম্বন হিসেবে তৈরি করা যায়। সেই সত্যটি হৃদয় দিয়ে আলিঙ্গন করতে হবে এবং প্রবাসী নেতৃত্বকেও বুঝতে হবে, নির্যাতন সহ্য করা ছাড়া আন্দোলন গড়ে ওঠে না। প্রবাস থেকে বাংলাদেশে এসে সগৌরবে কারাবরণ করে আন্দোলন বেগবান করতে হবে। প্রবাসে বিলাসী জীবনযাপন করে টেলিফোনের মাধ্যমে কোনো আন্দোলন সংগঠিত করা সম্ভব হয় না, সফলতা তো আসেই না।
লেখক : স্বাধীন বাংলা কেন্দ্রীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের আহ্বায়ক ও ছাত্রলীগের সাবেক সভাপতি। সূএ: বাংলাদেশ প্রতিদিন